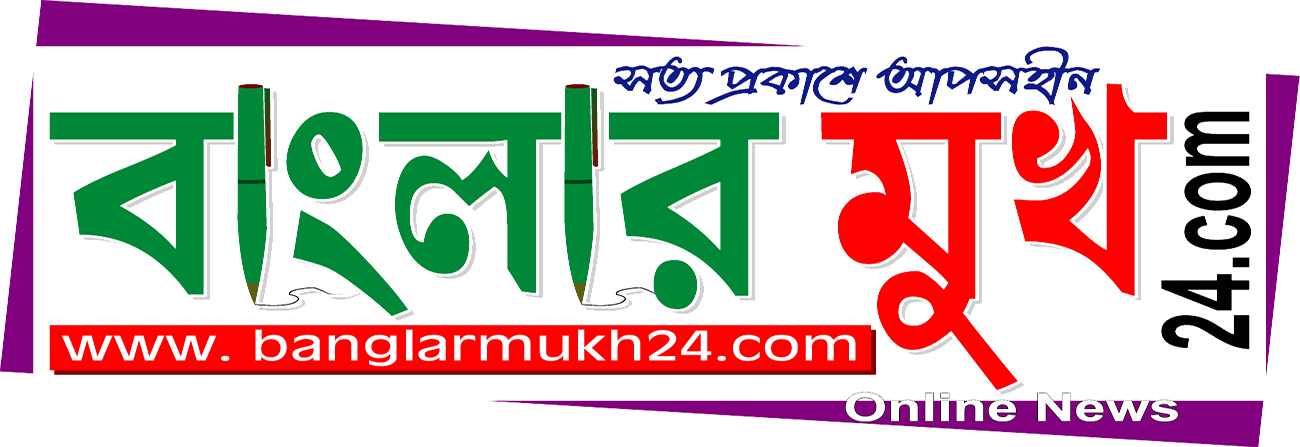অন্যতম কেন? কেনই–বা সেখানে আবার এত বাংলাদেশির মৃত্যু?
হাবিবুর রহমান: এই নগরীতেই জাতিসংঘসহ বহু বাণিজ্যকেন্দ্র অবস্থিত। তাই পুরো বিশ্ব থেকে লোক আসেন এখানে, বিমানবন্দরগুলো তুমুল ব্যস্ত থাকে। তবে বাংলাদেশিরা সংখ্যায় বেশি, তার কারণ হতে পারে একটু অপেক্ষাকৃত কম জায়গার মধ্যে বেশি মানুষ থাকে। গায়ানিজ, এশীয়, হিস্পানিকের মতো জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে বাংলাদেশিদের মৃত্যুহারটাই বেশি।
বাংলাদেশী ডাক্তার কেউ কি মারা গেছেন? অনেক চিকিৎসক আক্রান্ত, কিন্তু এত বেশি কেন?
হাবিবুর রহমান: আমার জানামতে, কেউ মারা যাননি। তবে আমার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অন্তত ছয়জন প্রবাসী বাংলাদেশি চিকিৎসক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তাঁদের চারজনই প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও অন্যরা হাসপাতালে করোনা রোগীর সংস্পর্শে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে তিনজনের অবস্থা এখনো সংকটাপন্ন। দুজন হাসপাতাল ছেড়ে দিন দুই হলো ঘরে ফিরেছেন। আমি রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, তাই চেনাজানা বলেই নয়, চিকিৎসক হিসেবেও আমার সঙ্গে তাঁদের সবার যোগাযোগ আছে। কেন তাঁরা আক্রান্ত হলেন, তার একটা ব্যাখ্যা এই যে তাঁরা করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসাকে ততটা গুরুত্ব হয়তো দেননি। সুরক্ষায় ঘাটতি ছিল।
এ সুরক্ষাটা নিউইয়র্কের হাসপাতালগুলো কীভাবে নিচ্ছে? আপনি কি সরাসরি রোগীর চিকিৎসা দিয়েছেন?
হাবিবুর রহমান: আমার সম্পৃক্ততা সরাসরি। বরং যাঁদের অবস্থা গুরুতর, যাঁদের আইসিইউতে রাখতেই হয়, তাঁদেরই তদারক করে আসছি। এ জন্য আমি তিন ধরনের মাস্ক পরি। প্রথমে এন–৯৫, তার ওপরে আরেকটি সাধারণ মাস্ক এবং চোখে আইশিল্ড। এর মধ্যে একজন রোগী থেকে আরেক রোগীর কাছে যাওয়ার সময় সাধারণ মাস্কটি ফেলে দিই। করোনার জীবাণু প্রধানত নাক, চোখ ও মুখ দিয়ে প্রবেশ করে। যাঁরা চশমা ব্যবহার করেন, তাঁরা এটা চশমার ওপরেই পরেন। আর মানসম্মত পিপিই তো আছেই। আমি বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে আশা করব, চিকিৎসকসহ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীরা দায়িত্ব পালনের সময় অবশ্যই এন–৯৫ বা সমমানের মাস্ক পরবেন। আর হাসপাতালের বাইরে তাঁরা সাধারণ মাস্ক পরবেন। যুক্তরাষ্ট্রেও পিপিই এবং মাস্ক সরবরাহে একটা টানাপোড়েন চলছে। আমরা সাধারণত পিপিই এবং এন–৯৫ এক দিনই ব্যবহার করতাম। সরবরাহ–সংকটের কারণে এন–৯৫ চার দিন পর্যন্ত পরেছিলাম কিন্তু সংকট কেটেও গেছে। মাথার ক্যাপ বদল করি প্রতিদিন।
আপনি বাসায় কী করছেন?
হাবিবুর রহমান: আমাদের পরিবারে চারজন চিকিৎসক। স্ত্রী, আমি ও আমার মেয়ে ও জামাতা। মেয়ে–জামাতা আলাদা থাকে। আমরা সবাই বাসাতেও সঙ্গনিরোধের নিয়ম মানছি। পরস্পর থেকে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখি। বিশেষ করে গত ১০ দিন হলো আমার স্ত্রী বাসাতেও মাস্ক পরছেন। খাবার টেবিলের এক প্রান্তে আমি, আরেক প্রান্তে স্ত্রী বসছেন। এটা ঘটেছে, কারণ আমার স্ত্রীর সহকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা যে যেখানেই আছি, একটা নিয়ম ধরে নিতে হবে যে করোনামুক্ত প্রমাণিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা সবাই সন্দেহভাজন জীবাণু বহনকারী।
বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন কি? প্রস্তুতি নিয়ে কী মনে হয়?
হাবিবুর রহমান: আমি মাঝেমধ্যে দেশে যাই। চিকিৎসক মহলের সঙ্গে মোটামুটি যোগাযোগ রাখি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিশ্বের সব বিশেষজ্ঞই একমত যে যত বেশি পরীক্ষা করা যাবে, তত বেশি সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। আমিও নিশ্চয় তা–ই মনে করি। যত দ্রুত এবং যত বেশি সম্ভব এই সামর্থ্য বাড়িয়ে যেতে হবে। পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু সময় যা হাতে আছে এবং বাংলাদেশের যা বাস্তবতা, তাতে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো প্রতিদিন ২০ হাজার মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা করানো সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে এ মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হতে পারে আইসোলেশন বাড়ানো। সামাজিক দূরত্ব সর্বাত্মকভাবে কার্যকর করতে হবে। এটা যত বেশি সার্থক ও সম্পূর্ণ করা যাবে, তত বেশি পরীক্ষা না করিয়ে বেশি সুফল পেতে পারে বাংলাদেশ।
প্রতিটি উপেজলায় যাঁরা লক্ষণযুক্ত, তাঁদের মধ্য থেকে দুজন করে পরীক্ষা করাতে চাইছে সরকার। কিন্তু লক্ষণ না থাকা ব্যক্তিরা কি নিরাপদ?
হাবিবুর রহমান: কার কখন করোনা হয়েছে, কার হয়নি, সেটা নির্ণয় করা খুব দুরূহ বিষয়। পরীক্ষা করে যে ফলই আসুক তার ওপর বেশি নির্ভর করা অর্থহীন হবে। কারণ পরীক্ষায় কারও নেগেটিভ ফল এল, তার মানেই যান্ত্রিকভাবে আপনি তাকে করোনামুক্ত বলতে পারেন না। তাই টেস্ট কিট কত বেশি মজুত আছে, বা কত বেশি মাত্রায় পরীক্ষা করা গেল, সেটাই ভরসার কথা নয়। অবশ্য নতুন প্রজন্মের কিট আসছে, যা আমাদের অধিকতর নির্দিষ্ট ফল দেবে। বিদ্যমান পিসিআর কিটের ফলের ওপর ৬০–৭০ শতাংশ এবং বাকি ৩০–৪০ শতাংশ ঘাটতির পূর্ণতা দেবেন চিকিৎসক। কিটের সঙ্গে তাই আপনার উপযুক্ত চিকিৎসক থাকতে হবে। একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যতথ্য, সিটি স্ক্যান বা এক্স–রে রিপোর্ট এবং চলতি সিম্পটম চিকিৎসকের জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এসবের ভিত্তিতে তিনি পিসিআর পরীক্ষার আগেই তিনি পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন যে তার কেসটি কোভিড–১৯। তাই তিনি যদি দেখেন যে টেস্টের ফল নেগেটিভ, তাহলেও চিকিৎসক অটল থাকবেন এবং ঘোষণা দেবেন যে তাকে করোনায় ধরেছে।
আগে যে বাংলাদেশি চিকিৎসকদের কথা বললাম, তাঁদের কিছুটা অমনোযোগী হওয়ার আরেকটি কারণ এই ছিল যে রোগী যারা এসেছিলেন, তাঁরা কোনো লক্ষণ নিয়ে আসেননি। তাঁরা ছিলেন নীরব বহনকারী। হয়তো সামান্য কাশি নিয়ে এসেছেন। তাই তাঁদের মূল্যায়নে ঘাটতি ছিল। যাঁরা সাইলেন্ট ক্যারিয়ার তাঁরা আরেকটি ঘটনা ঘটাতে পারে। তাঁর মাধ্যমে যিনি আক্রান্ত হলেন, তাঁর শরীরে লক্ষণ হোস্টের আগে প্রকাশ পেতে পারে। অথচ হোস্ট অসচেতন থাকবেন যে তিনি বহন করছেন। এভাবে তিনি তাঁর পরিবারের আপনজনদের মধ্যে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটিয়ে চলতে পারেন।
তবে ১৪ দিনের মধ্যেই লক্ষণ প্রকাশের বিষয়টি কি স্বতঃসিদ্ধ?
হাবিবুর রহমান: মোটামুটিভাবে ১৪ দিন ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি এটা শতভাগ নিশ্চিত বলব না।